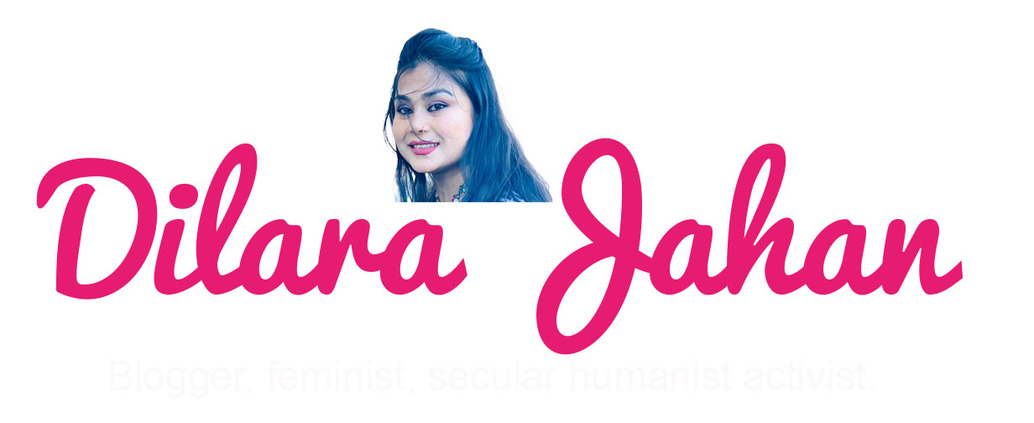ন্যায়বিচার হলো সেই আলো, যা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার এবং যার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনসম্মতভাবে, নিরপেক্ষভাবে ও ভয়হীনভাবে তাঁর অভিযোগ জানাতে পারেন এবং শুনানির অধিকার পান। এটি একটি সর্বজনীন নৈতিক আদর্শ, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদেও প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এই ন্যায়বিচার যদি শর্তসাপেক্ষ হয়—যেমন যৌতুক বা সহিংসতার অভিযোগ আনতে গেলে একজন নির্যাতিত নারীকে বিচারের আগে তাঁর নির্যাতকের সঙ্গে মধ্যস্থতার জন্য এক টেবিলে বসতে হয়, তাহলে সেই আলোর রং কি সত্যিই খাঁটি থাকে?
২০২৫ সালের সংশোধিত আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০-এ এমনই এক শর্ত সংযুক্ত হয়েছে। এখন থেকে পারিবারিক বিরোধ, যৌতুকের অভিযোগ (ধারা ৩ ও ৪) এবং নারী নির্যাতনের অভিযোগ (১১ [গ] ধারা) আদালতে দায়েরের আগে বাধ্যতামূলকভাবে ‘বসে সমঝোতা’ করার চেষ্টা করতে হবে।
আইনটি প্রথম শুনতে নিরীহ বা ‘ঝামেলা কমানোর উদ্যোগ’ মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এ আইনি কাঠামো নারীকে বিচার পাওয়ার পূর্বে এক অসম লড়াইয়ে ঠেলে দিচ্ছে। একজন নারী যখন নিজের ওপর সংঘটিত সহিংসতার বিচার চাইতে যান, তখন তাঁকে বলা হচ্ছে, ‘তুমি আগে অপরাধীর সঙ্গে বসো, সমঝোতা করো, তারপর বিচার হবে।’
এটি শুধু অমানবিক নয়, এটি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আমাদের সামাজিক বাস্তবতায়, যেখানে নারীরা পুরুষতান্ত্রিক চাপ, পারিবারিক নির্ভরতা এবং সমাজের অপবাদে জর্জরিত; সেখানে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা নারীর জন্য দ্বিতীয় দফা নির্যাতনের মতোই নির্মম। বিচারের আগে এই ‘বসা’ আদতে ভিকটিমের জন্য অনিচ্ছাকৃত সমঝোতার এক পরোক্ষ চাপ। এই চাপ কখনো আসতে পারে পারিবারিক ইজ্জতের দোহাই দিয়ে, কখনো মধ্যস্থতাকারীর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে, আবার কখনো ভুক্তভোগীর নিজস্ব অসহায়তার কারণে।
এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ওঠে—একজন নারী যদি সরাসরি আদালতে মামলা করতে চান, তাহলে কেন তাঁকে একটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে? এখানে আরও গুরুতর একটি দিক হলো যৌতুক মামলা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১১ (গ) ধারা—এসব স্পষ্টভাবে ফৌজদারি অপরাধ। এই অপরাধগুলো কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধের ওপর আঘাত। এসব অপরাধে রাষ্ট্র নিজেই পক্ষ হয়ে মামলা পরিচালনা করতে পারে। এমন অবস্থায় ভিকটিমকে অপরাধীর পাশে বসাতে বাধ্য করা আইন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।
বিচারপ্রার্থী নারীকে মামলার আগে অপরাধীর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে মধ্যস্থতার জন্য বসতে বলা ন্যায়বিচারের মূল চেতনার পরিপন্থী। একজন নারী যখন যৌতুক, সহিংসতা বা নির্যাতনের মতো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে আদালতের দ্বারে যেতে চান, তখন তাঁকে অপরাধীর মুখোমুখি বসতে বাধ্য করা মানে তাঁর ওপর রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বিতীয়বার নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া।
এই বাস্তবতায় আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোতেও স্পষ্ট বার্তা পাই। সিডওর (সিইডিএডব্লিউ) নারীর প্রতি বৈষম্যের বিলোপসংক্রান্ত সনদের ৩৩ নম্বর সাধারণ সুপারিশে বলা হয়েছে: ‘রাষ্ট্রের এটি নিশ্চিত করা উচিত যে সহিংসতার শিকার নারীকে, বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া কোনো নারীকে তাঁকে জোর করে সমঝোতা বা আপসে যেতে বাধ্য করা যাবে না।’
এখানে ‘কনসিলিয়েশন’ বা মেডিয়েশন’ বলতে আপস, সমঝোতা বা বিচারবহির্ভূত মীমাংসার কথা বোঝানো হয়েছে। সিডও বলছে, এসব ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি ছাড়া কোনো রকম আপস চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এ ছাড়া ইউএন উইমেনের ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুসারে, এমন বাধ্যবাধকতা একজন নারীকে আবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে, যার ফলে তিনি ন্যায়বিচার চাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলতে পারেন।
এ ছাড়া বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও এই আইনের প্রয়োগ নারীর জন্য অনিরাপদ হতে পারে। অধিকাংশ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে মাত্র একজন অফিসার কাজ করেন। তার ওপর রয়েছে মিডিয়েশন পরিচালনা, আবেদন যাচাই, আইনজীবী নিয়োগ, ফাইলিং, রিপোর্টিং ইত্যাদি বহুবিধ দায়িত্ব। ফলে একটি সংবেদনশীল মামলা যথাযথ শোনা বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার ওপর বহু অফিসে নেই আলাদা কক্ষ, প্রশিক্ষিত নারী মিডিয়েটর বা ট্রমা সংবেদনশীলতা বিষয়ক গাইডলাইন। এমন এক ব্যবস্থায় একজন নির্যাতিত নারী কীভাবে তাঁর বিচার পাওয়ার আত্মবিশ্বাস ধরে রাখবেন?
পরিশেষে বলতে পারি, বিচারপ্রার্থী নারীকে মামলার আগে অপরাধীর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে মধ্যস্থতার জন্য বসতে বলা ন্যায়বিচারের মূল চেতনার পরিপন্থী। একজন নারী যখন যৌতুক, সহিংসতা বা নির্যাতনের মতো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে আদালতের দ্বারে যেতে চান, তখন তাঁকে অপরাধীর মুখোমুখি বসতে বাধ্য করা মানে তাঁর ওপর রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বিতীয়বার নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া। এই অবস্থায় মধ্যস্থতা যদি থাকেই, তবে তা নারীর সম্মতি ও সুবিধার ভিত্তিতে ঐচ্ছিক হওয়া উচিত। তাই এ আইন বাস্তবায়ন করতে হলে তা বাধ্যতামূলক নয়; বরং বিকল্প পথ হিসেবে রাখা উচিত, যেখানে ভিকটিম চাইলে বসতে পারবেন, না চাইলে সরাসরি বিচারিক প্রক্রিয়ায় যেতে পারবেন।
এতে বিচারপ্রার্থী নারী যেমন নিরাপদ বোধ করবেন, তেমনি বিচারিক মর্যাদাও বজায় থাকবে। বিচার কখনো কারও করুণা নয়, এটি অধিকার। আর অধিকার কখনোই শর্তসাপেক্ষ হওয়া উচিত নয়।
সুত্র: প্রথম আলো